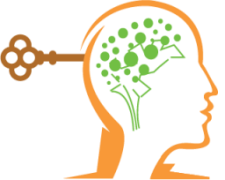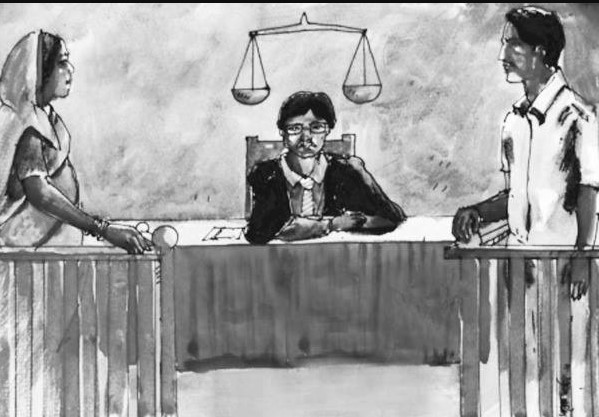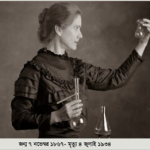বাংলাদেশের পারিবারিক আইন এ নারীর অবস্থান
-মর্জিনা খাতুন
নারী অধিকার আন্দোলনের কর্মী
পারিবারিক বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা থেকে যে আইন তাই পারিবারিক আইন নামে পরিচিত। পারিবারিক বিষয়াদি যেমন-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব নির্ধারণ ও উত্তরাধিকার বিষয়াদি এই আইনের অন্তর্ভক্ত। আইন মূলত একটি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। আমাদের দেশের এই পারিবারিক আইন বৈষম্যমূলক ।
অন্যান্য দেওয়ানি – ফৌজদারি আইনে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক না হলেও এই পারিবারিক আইনে বৈষম্য রয়েছে। কারণ আমরা যে রাষ্ট্রে বাস করছি তা একটি বৈষম্যমূলক রাষ্ট্র। এখানে নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, ধর্মে- গোত্রে বৈষম্য রয়েছে।
সেজন্য আমাদের সংগ্রাম শুধু পারিবারিক আইন পরিবর্তনের জন্য নয়, যে বৈষম্যের কারণে এই বৈষম্যমূলক আইনের সৃষ্টি তার মূল উৎপাটন করা। আমরা নারীরাপ্রধানতদুইটি বিষয়কে সামনে রেখে লড়াই করছি- ১.পুরুষতান্ত্রিক মাসনসিকতা ও ২. পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তি। পুরুষতান্ত্রিক মাসনিকতা হলো সেই পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে নারীকে হেয় করে দেখা হয়। বিদ্যমান এই সমাজ প্রথা, রীতিনীতি, আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিএই মানসিকতাকে টিকিয়ে রেখেছে।
আর উৎপাদনের হাল-হাতিয়ার মালিকরা নিজেদের দখলে রেখে পুঁজির শোষণকে টিকিয়ে রাখছে। ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এই শোষণের শিকার হলেও অধঃস্তনতার কারণে নারী বেশি শোষণের শিকার। তাই সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করে অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইউনিফরম সিভিল কোড প্রতিষ্ঠা অতীব জরুরী।
কারণ বাংলাদেশের এই পারিবারিক আইন ধর্মীয়-বিধান থেকে এসেছে। যদিও বিভিন্ন সময়ে এর পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধন হয়েছে। যেমন ১৯৬১ সালের পূর্বে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে এতিম সন্তানরা বাবা-মা মারা গেলে পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ ও মাতামহীর সম্পত্তিতে অংশীদার হত না। কিস্তু ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে সম্পত্তিতে এতিম সন্তানদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হয়।
হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহ আইন ১৯৬৫ পাস করা হয়। খিস্ট্রান ধর্মের আইনেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু সম্পত্তিসহ পারিবারিক আইনে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরেও উপেক্ষিত।
আবার সিডও সনদের পূর্ণস্বীকৃতি ও বাস্তবায়নের দাবি নারী সমাজের পক্ষ থেকে বার বার উত্থাপন করা হলেও সরকার তা উপেক্ষা করছে। আসলে এই দাবির যৌক্তিকতা কি ?সরকার ১৯৮৪ সালে ২ও ১৬ (১ )(গ) সংরক্ষণ রেখেসিডও সনদ স্বাক্ষর করেছে। কারণ অনুচ্ছেদ ২ এ নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য বিলোপ এবং ১৬(১) (গ) তে বিবাহ ও বিচ্ছেদকালে নারী এবং পুরুষের একই অধিকার এবং দায়িত্ব এর কথা বলা হয়েছে ।
সিডও সনদের এই অনুচ্ছেদ সংরক্ষণ রেখে সরকার বিদ্যমান পারিবারিক আইনেও বৈষম্য বহাল রেখেছে। যেহেতু পারিবারিক আইনধর্মভিত্তিক সেজন্য নারীসমাজের পক্ষ থেকে সম্পত্তিসহ সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উঠলেও সরকার সেই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছে বার বার। প্রতিটি সরকার যেহেতু ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করে সেজন্য বৈষম্যমূলক এই আইন পরিবর্তনে তারা কোন ভূমিকা পালন করে না।
অথচ সংবিধানের ২৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা আছে – কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী,বর্ণ-নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। কিন্তু পারিবারিক আইন সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের লংঘন বলে নারীসমাজ মনে করে। বিদ্যমান এই পারিবারিক আইন কিভাবে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা তা পারিবারিক আইনের আলোচনায় আমরা দেখবো।
মুসলিম পারিবারিক আইন
শরীয়া আইন থেকে মুসলিম পারিবারিক আইনের উৎপত্তি হলেও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ও বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে বিভিন্ন সময় নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করা হয়েছে।
এই ধরণের কয়েকটি আইন হলো-মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১,মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৭৪ এবং বিধিমালা ১৯৭৫, মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯ ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে উচ্চ আদালতের দেয়া সিদ্ধান্ত ও আইনের ব্যাখ্যা এ আইনের ক্ষেত্র বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
এই প্রবন্ধে মুসলিম পারিবারক আইনের কতিপয় বিষয় যেমন-বিবাহ ও বিবাহের শর্ত, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার ইত্যাদি আলোকপাত করা হবে।
মুসলিমআইনে বিবাহ
আইন অনুসারে মুসলিম বিবাহ একটি সামাজিক ও দেওয়ানী চুক্তি। এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন স্বাধীন মানুষের প্রয়োজন। ফলে দু‘জন সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন নারী-পুরুষ নিজেদের মতামতের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বৈধভাবে জীবন-যাপনের জন্য সামাজিকভাবে যে চুক্তি করে তাকে মুসলিম বিবাহ বলে।
বিবাহের শর্ত:
মুসলিম আইন অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ বিবাহের জন্য যে শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে তা হলো – ১. বয়স, ২. সম্মতি, ৩. দেনমোহর, ৪. সাক্ষী এবং ৫.রেজিস্ট্রেশন।
১. বয়স: বিবাহের জন্য মেয়ের বয়স ১৮ বছর ও ছেলের বয়স ২১ বছর পূর্ণ হতে হবে।
২. সম্মতি: বিবাহের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে বর ও কনের সম্মতি যা স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে দিতে বা নিতে হবে। জোর করে বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বা প্রলোভন দেখিয়ে সম্মতি আদায় করা আইনে গ্রহণযোগ্য নয়। সম্মতি ব্যতিত জোরপূর্বক বা প্রতারণামূলকভাবে বিবাহ দিলে তা বাংলাদেশ দন্ডবিধি অনুযায়ী ১৪ বৎসর পর্যন্ত কারাদ-, জরিমানা অথবা উভয় শাস্তিই হতে পারে।
৩. দেনমোহর:দেনমোহর মুসলিম বিয়ের অন্যতম শর্ত। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বিবাহের চুক্তির শর্তানুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ দেয়া বা দেয়ার অঙ্গীকার করাই দেনমোহর।দেনমোহর পরিশোধ করতে স্বামী আইনতঃ বাধ্য।
বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী দেনমোহর আদায় করে নিতে পারবে। স্বামী কোন কারণে দেনমোহর পরিশোধ না করলে স্ত্রী আদালতের আশ্রয় নিতে পারবে। মূলত দুইভাবে দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে। বিবাহের আসরে তাৎক্ষণিক ভাবে বা স্ত্রী চাহিবামাত্র স্বামী দেনমোহর পরিশোধ করবেন। এছাড়া বিবাহিত জীবনের যেকোন সময় এবংবিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পরও দেনমোহর পরিশোধ করা যাবে।
৪. সাক্ষী :বিবাহে ছেলে ও মেয়ে স্বেচ্ছায় সম্মতি দিয়েছে কিনা তা যাচাই করা সাক্ষীদের কাজ। বিয়েতে দুইজন প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন মানুষ সাক্ষী হিসেবে থাকতে হবে।
৫. বিবাহ রেজিস্ট্রেশন : ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন (৫২নং আইন) অনুযায়ী প্রতিটি মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন বিবাহের একটি দলিল যা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং লাইসেন্সধারী কাজী দ্বারা সম্পাদিত, যেখানে বর ও কনের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমুহ- বিবাহ আসরেই বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে হবেবিবাহ সম্পাদনের ৩০ দিনের মধ্যে বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে হবে।
নিকাহনামা/ রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা:নিকাহ্নামার সকল কলাম বিবাহের আসরেই যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে কিনা তা দেখে বর, কনে, সাক্ষী ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর দিতে হবে।বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট কোন সমস্যার কারণে আদালতের আশ্রয় নিতে হলে বিবাহ চুক্তির প্রমাণ হিসেবে রেজিস্ট্রিকৃত কাবিননামা আদালতে জমা দিতে হবে।
যেমন – স্ত্রী- সন্তানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ভরণপোষণ না দিলে, স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে আরেকটি বিয়ে করলে বা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেনমোহর থেকে বঞ্চিত করলে, প্রতারণা করে বিবাহিত থাকা অবস্থায় আর একটি বিবাহ করলে রেজিস্ট্রিকৃত নিকাহ্নামা অবশ্যই প্রয়োজন।
নিকাহনামা/ আসল কাবিননামা:নিকাহ্নামা / আসল কাবিননামা হালকা নীল রং ফর্ম যার নম্বর ১৬০০ এবং এই ফরমে ২৫টি কলাম আছে। প্রতিটি কলাম পূরণ করতে হবে।
নিকাহ্নামার/কাবিননামার প্রতিলিপি:নিকাহ্নামার প্রতিলিপি বা নকলকপি যার নম্বর ১৬০১ যা বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর নিকাহ্ রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট দুইপক্ষকে রেজিস্ট্রারে অন্তর্ভূক্তির পর সত্যায়িত নকলকপি প্রদান করবে।
বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদানের রশিদ : বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর রেজিস্ট্রেশন ফি গ্রহণের জন্য একটি রশিদ প্রদান করতে হবে, যার নম্বর ১৬১৬।
বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ফি:বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করার জন্য সরকার কতৃক নির্ধারিত কাজী বা নিকাহ্ রেজিস্টার আছে। নিকাহ্ রেজিস্টার বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রতি হাজার দেনমোহরে বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ১২.৫০ (বার টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা হারে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ফি আদায় করতে পারবেন।তবে দেনমোহরের পরিমাণ ৪(চার) লক্ষ টাকার অধিক হলে পরবর্তী এক লক্ষ টাকা দেনমোহর বা উহার অংশবিশেষের জন্য একশত টাকা বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ফি আদায় করতে পারবেন।
তবে দেমোহরের পরিমাণ যাহাই হোক না কেন সর্বনিম্ন ফি ২০০(দুইশত) টাকার কম হবে না।বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ফি আইনত স্বামীকে পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া কাজী বিবাহ রেজিস্টেশণ ফরম যাচাই-বাছাই করে সঠিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসন বা জেলা রেজিস্টার বরাবর আবেদন করা যাবে।
বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করার শাস্তি : বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করলে ২ বছরের কারাদ- বা ৩,০০০/- টাকা জরিমানা বা উভয় শাস্তি হবে। বিবাহের আয়োজনকারি , বর/কনে পক্ষের লোকজন এবং যিনি বিবাহ সম্পন্ন করবেন সকলের এই শাস্তি হবে।
উল্লেখ্য যে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ প্রতারিত বা হয়রানির শিকার হয়। নিকাহনামার আসল কপি ও নকলকপির মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা, ফি গ্রহণের রশিদ না চেনা, কাজীর নির্দিষ্ট ফি না জানার কারণে অতিরিক্ত ফি আদায়সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ প্রতারিত হয় বলে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা গুরুত্বপূর্ণ।
বিবাহরেজিস্ট্রেশন ফরমের “৫ ও ১৮ নম্বর ঘর“ এর বক্তব্য নারীর প্রতি চরম বৈষম্যমূলক
বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ফরমের ‘৫নম্বর ঘর‘ এ বলা হয়েছে -কন্যা কুমারী, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্ত নারী কিনা? নারীর ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন করা হলেও পুরুষের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য প্রযোজ্য করা হয়নি। আমাদের সংবিধানেরতৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকার অংশের অনুচ্ছেদ ২৭ বলা হয়েছে – সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী এবং অনুচ্ছেদ-২৮(১) বলা হয়েছে – কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরূষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। তাহলে রেজিস্ট্রেশন ফরমের এই বক্তব্য কি সংবিধানের লংঘন নয় ?
যে সংবিধান মেনে এই রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সেই সংবিধানের মৌলিক অধিকার লংঘন করে বিবাহের রেজিস্ট্রেশন ফরমের এই ধরনের বক্তব্য বাতিল করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি নারী-পুরষ উভয়ের ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রশ্ন থাকা উচিৎ। শুধু নারীর ক্ষেত্রে নয়। একইভাবে ‘১৮ নং ঘর‘এ বলা হয়েছে- স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে কিনা?
করিয়া থাকিলে কী কী শর্ত? এই কলামটিও নারী-পুরুষের সমমর্যাদার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক এবং সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। কারণ বিবাহ দইুজন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন মানুষের চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ করার অধিকার দুইজনের সমান হওয়া উচিৎ। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও পুরুষের ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয়ে স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হয়েছে।
বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পুরুষের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। চুক্তি অনুযায়ি বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি গণতান্ত্রিক অধিকার – এই অধিকার মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ বা স্বামী-স্ত্রী দুইজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত।
মুসলিম আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ
মুসলিম পারিবারিক আইনে বিবাহ একটি দেওয়ানী ও সামাজিক চুক্তি।তাই বিবাহের মাধ্যমে স্থাপিত সম্পর্ককে আইনসিদ্ধ উপায়ে বিচ্ছেদ করাকে বিবাহ বিচ্ছদ বলে। বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামী নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রয়েছে। স্ত্রী কিছু আইনগত শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে। বিবাহ- বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সমান নয়। স্বামী বা স্ত্রী যেভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে তা নি¤œরূপ:
ক. স্বামীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ: স্বামী নিজের ইচ্ছায় যখন খুশি তখন বিচ্ছদ ঘটাতে পারে। তার এই একচ্ছত্র ক্ষমতাকে তালাক বলে।
খ. স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ: স্ত্রী নি¤েœাক্ত পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে(শর্ত সাপেক্ষে) বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।
স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করলে যাকে তালাক-ই-তৌফিজ বলে( বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ১৮ নং ঘর এর বক্তব্য অনুযায়ী)
খুলার মাধ্যমেঅর্থাৎ স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে
মুবারতের মাধ্যমে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী দুইপক্ষের সম্মতিতে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।
আদালতের মাধ্যমে
স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক
একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থমস্তিষ্কের মুসলিম পুরুষ যেকোন সময় তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। তবে যখন খুশি তখন মুখে বলে বা লিখিত দিলে তালাক হবে না। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে তালাক প্রদানের জন্য সুনির্ধারিত ও সুনিদিষ্ট পদ্ধতি বলা আছে। এই অধ্যাদেশ- এর ৭(১) ধারায় বলা হয়েছে-
ক্স কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে স্ত্রী যে ইউনিয়নে বসবাস করেন সেই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট তালাকের লিখিত নোটিশ পাঠাতে হবে। স্ত্রীকেও নোটিশের একটি কপি পাঠাতে হবে। এই আইনে চেয়ারম্যান বলতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার চেয়ারম্যান, মেয়র প্রভৃতি ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে।
ক্স চেয়ারম্যান নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে উভয় পক্ষের ২ জন মনোনীত প্রতিনিধি এবং তিনি অথবা তার মনোনীত একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে সালিশী পরিষদ গঠন করবেন। সালিশী পরিষদ উভয়পক্ষকে ডেকে সমঝোতার চেষ্টা করবে। সমঝোতার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর পুণর্মিলন হলে তালাক কার্যকরী হবে না।
ক্স সালিশীতে উভয়পক্ষ সমঝোতায় না আসলে চেয়ারম্যান নোটিশ পাওয়ার ৯০ দিন পর তালাক কার্যকরী হবে। ৯০ দিন পার না হওয়া পর্যন্ত দম্পতিকে আইনসিদ্ধ স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই ধরা হবে এবং স্ত্রী ভরণপোষণও পাবে।
তালাক কখন কার্যকরী হবেনা :স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় স্বামী তাকে তালাক দিলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকরি হবে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে তালাক কার্যকরি হবে।
বিচ্ছেদ প্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ : ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী তালাকের মাধ্যমে কোন বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে, এই আইনের ৭(৬) ধারা মোতাবেক তিনবার তালাক কার্যকরী না হলে তালাক হওয়া দম্পতি পুনরায় বিবাহ করতে চাইলে নতুনভাবে বিবাহ করতে পারবে। এর জন্য স্ত্রীকে মধ্যবর্তীকালিন কোন বিয়ে/ হিলা বিয়ে দিতে হবে না।
চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান ব্যতিত তালাকের শাস্তি: কোন ব্যক্তি তালাকের নোটিশ সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানকে না দিলে সেই ব্যক্তি ১(এক) বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদ- অথবা ১০,০০০/(দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দ-ে দ-িত হবেন। উল্লেখ্য যে চেয়ারম্যানকে নোটিশ না দিলে তালাক কার্যকর হবে না।
স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক
ক. তালাক-ই-তৌফিজের মাধ্যমে অর্থাৎ বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ১৮ নং ঘর-এর বক্তব্য অনুযায়ী স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করলে:তালাক-ই-তৌফিজ স্ত্রীর নিজস্ব ক্ষমতা নয়। স্বামী যদি কাবিননামার ১৮ নং কলামের মাধ্যমে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেন, তবে স্ত্রীও স্বামীর মতো তালাক দিতে পারবে।
সেক্ষেত্রে স্ত্রীকেও তালাকের নোটিশ চেয়ারম্যানের কাছে এবং এর কপি স্বামীর কাছে পাঠাতে হবে। স্ত্রীর এই তালাক দেওয়ার ক্ষমতাই হলো তালাক-ই-তৌফিজ। নিকাহ্নামার ১৮ নং ঘর-এ উল্লেখ করা হয়েছে ‘ স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেছে কিনা ? করে থাকলে কী কী শর্তে?’ এই প্রশ্নটি থাকে।
এই পদ্ধতিতে স্ত্রীর তালাক দেয়ার ক্ষমতা কেবল তখন ঠিক হয়, যখন স্বামী নিকাহ্নামার ১৮ নয় ঘরে কিছু কারণ ও ক্ষেত্র নিদিষ্ট করে দিয়ে স্ত্রীকে এই ক্ষমতা প্রদান করেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, স্বামী যদি ১৮ নং ঘরটি পূরণে আপত্তি করেন বা “না“ উল্লেখ করেন বা কোনো ক্ষেত্র উল্লেখ না করেন বা দু’তিনটি বা একটি ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রদান করেন তখন স্ত্রীর তালাক প্রদান করার ক্ষমতা সীমিত হবে। নিকাহ্নামায় নারী-পুরুষ সমভাবে একে অপরকে তালাক দেয়ার অধিকার পাবে এই বক্তব্য থাকাই বাঞ্চনীয়। ফলে নিকাহ্নামার এই বক্তব্যটি নারী-পুরুষের সমনাধিকারের ধারণার পরিপন্থি এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক।
খ. খুলা বিচ্ছেদ
মুসলিম অইনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক মতবিরোধ হলে বিবাহ-বিচ্ছদ ঘটাতে পারে। তবে খুলার মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রস্তাব আসে স্ত্রীর পক্ষ থেকে। স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে (সাধারণত দেনমোহর বা অন্য কোনো মূলবান সম্পত্তি) স্বামীকে বিচ্ছেদ ঘটাতে রাজী করানোর চেষ্টা করতে পারেন। এক্ষেত্রে স্ত্রী চেয়ারম্যানকে তালাকের নোটিশ পাঠাবেন।
গ.মোবারাত
যে ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং তারা উভয়েই চুক্তির মাধ্যমে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চান,সেই পদ্ধতি মোবারাত। তবে মোবারতে স্ত্রীকে কোনো কিছু পরিত্যাগ করতে হয় না। যেকোন একপক্ষ প্রস্তাব উত্থাপন করেন, অপরজন প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে যিনি প্রস্তাব উত্থাপন করবেন তিনি চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ প্রেরণ করবেন।
ঘ. আদালতের মাধমে
‘মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯’ অনুসারে কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট কারণে স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দিতে পারবে। এসব কারণের জন্য স্ত্রীকে আদালতে আবেদন করতে হবে।
‘মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯’ – এর ধারা ১ অনুসারে কোনো বিবাহিত স্ত্রী এক বা একাধিক কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী হয় এগুলো হলো —
১. স্বামী যদি ৪ বছরের বেশী সময় নিরুদ্দেশ থাকে
২. স্বামী যদি দুই বছর যাবৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ না করে
৩. ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান লঙ্ঘন করে স্বামী যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে
৪. ৭ বৎসর বা তার চেয়ে বেশি সময় স্বামী কারাদ-ে দ-িত হলে
৫. কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তিন বছর যাবৎ স্বামী তার দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে
৬. স্বামী বিয়ের সময় পুরুষত্বহীন থাকলে এবং তা মামলা চলাকালীন সময় পর্যন্ত বজায় থাকলে
৭. স্বামী যদি দুই বছর যাবৎ মানসিক প্রতিবন্ধি থাকে অথবা কুষ্ঠব্যধিগ্রস্থ বা মারাত্মক যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে
৮. নাবালিকা অবস্থায় বিবাহ হয়ে থাকলে সাবালকত্ব লাভের পর অর্থ্যাৎ ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর স্ত্রী যদি বিয়ে অস্বীকার করে
৯. এছাড়াও স্বামী যদি স্ত্রীকে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করে, স্বামী যদি অনৈতিক জীবন যাপন করে এবং স্ত্রীকে অনৈতিকত জীবন যাপনের জন বাধ্য করার চেষ্টা করে, স্ত্রীর সম্পত্তি হস্তান্তর করে কিংবা স্ত্রীকে তার সম্পত্তির উপর বৈধ অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেয়, স্ত্রীকে তার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে বাঁধা দিলে এবং স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকে ও তাদের সাথে সমান ব্যবহার না করলে স্ত্রী এক বা একাধিক কারণে আদালতের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব স্ত্রীর। অভিযোগ প্রমাণিত হলে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ পেতে পারেন। আদালত বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি দেয়ার পর সাতদিনের মধ্যে ডিক্রির সত্যায়িত কপি আদালতের মাধমে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের কাছে পাঠাতে হবে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ অনুযায়ি চেয়ারম্যান নোটিশটিকে তালাক সংক্রান্ত নোটিশ হিসেবে গণ্য করে আইনানুযাযী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। চেয়ারম্যান যেদিন নোটিশ পাবেন সেদিন থেকে ঠিক নব্বই দিন পর তালাক চূড়ান্ত হবে।
স্বামীর অবস্থান জানা না থাকলে মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯ এর ধারা ৩ অনুসারে তার উত্তরাধিকারগণের কাছে নোটিশ দিতে হবে। এই আইনের ৫ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, এই প্রক্রিয়া নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে মুসলিম আইনানুসারে তার দেনমোহর বা এর কোনো অংশের ওপর কোনো অধিকারকেই প্রভাবিত করবে না।
তালাক রেজিস্ট্রেশন: ‘মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রিকরন আইন ১৯৭৪’অনুসারে বিবাহের মতো তালাকও রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ২০১১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখের গেজেট নোটিফিকেশন অনুয়ায়ি, যে কোন ধরনের তালাক রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রার বা কাজীকে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ফি প্রদান করে তালাক রেজিস্ট্রি করতে হবে। আইনানুসারে যে ব্যক্তি তালাক কার্যকর করেছেন সে ব্যক্তি তালাক রেজিস্ট্রি করার জন্য আবেদন ও ফি জমা দিবেন।
মুসলিম পারিবারিক আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ বৈষম্যমূলক
মানবাধিকার সনদ স্বাক্ষরকারি দেশ হিসাবে রাষ্ট্র মানবাধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ১৬ এর (ক) কে লংঘন করেছে। এই ধারায় বলা হয়েছে – পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের জাতিগত, জাতীয়তা অথবা ধর্মের কারণে কোন সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে বিবাহ করা ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে তাদের সমঅধিকার রয়েছে।
একই ভাবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৮(১) বলা হয়েছে – কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরূষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। অথচ বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনে নারীর প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দূর করে নারীর সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের কর্তব্য।
মুসলিম আইনে ভরণপোষণ
বেঁচে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক চাহিদার পূরণই ভরণপোষণ । আর্থিক দিক দিয়ে এই ভরণপোষণ কত হবে তা নির্ধারিত নেই। সমাজিক মর্যাদা এবং অন্যান্য প্রেক্ষিতের বিবেচনায় ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। একজন সক্ষম ও উপার্জনশীল ব্যক্তি স্ত্রীর এবং নাবালক সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ করতে বাধ্য।
স্ত্রীর ভরণপোষণ: মুসলিম আইন অনুযায়ি বিবাহ একটি চুক্তি। এই বিবাহের ফলে কিছু আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। যার মধ্যে ভরণপোষণ অন্যতম। ভরণপোষণ স্বামীর দায়িত্ব ও স্ত্রীর অধিকার। বিয়ের কারণে থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ও জীবনধারণের অন্যান্য উপকরণ স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে পাওয়ার অধিকারি। এই অধিকার যেমন বিবাহ থাকাকালীন অবস্থায় বর্তমান থাকে তেমনি বিবাহ বিচ্ছেদকালীন সময়েও বিদ্যমান থাকে। তবে এই অধিকার সীমিত এবং সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য বিদ্যমান থাকে।
মুসলিম আইনে স্বামীর জন্য কিন্তু স্ত্রীকে এই ধরণের দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয় না। কারণ ধরে নেওয়া হয় যে, মেয়ে বাবা ও স্বামীর উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল। তাই স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবে । স্ব^ামীর ভরণপোষষের দায়িত্ব স্ত্রীর উপর বর্তায় না।
যেসব ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে আলাদা বসবাস করেও ভরণপোষণ পাবে
ক্স স্বামী যদি স্ত্রীর দেনমোহরের তাৎক্ষণিক অংশ পরিশোধে অস্বীকার করে বা পরিশোধ না করে
ক্স স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে
ক্স স্বামী যদি স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করে সেক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর সাথে একত্রে বসবাসে অস্বীকৃতি জানাতে পারে এবং ভরণপোষণ দাবি করতে পারে।
বিবাহ- বিচ্ছেদের পর কতদিন স্ত্রী ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী: যেদিন থেকে তালাক কার্যকর হয় সেদিন থেকে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবে অর্থাৎ ইদ্দতকালিন সময়ে স্ত্রী ভরণপোষণ পাবে। মূলত: এই আইন করার কারণ স্ত্রী সন্তানসম্ভবা কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য।
স্ত্রী কিভাবে স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ আদায় করতে পারবেন – ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ অনুযায়ি ৪৮৮ ধারা অনুযায়ি আদালত সর্বোচ্চ মাসিক ৫০০ টাকার সমপরিমাণ ভরণপোষণ দেয়ার আদেশ দিতে পারে। এছাড়া ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৯ ধারা অনুযায়ী স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হলে স্ত্রী স্থানীয় চেয়ারম্যানের নিকট এ বিষয়ে আবেদন করবেন।চেয়ারম্যান সালিশী পরিষদ গঠন করে সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী ভরণপোষণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিবেন এবং এই মর্মে তিনি একটি সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভরণপোষণ এর জন্য নির্ধারিত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ না করলে তা বকেয়া ভূমি রাজস্বের মতো আদায় করা হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হলে তিন মাসের (ইদ্দতকাল পর্যন্ত) ভরনপোষণ পাবেন। কোনো ব্যক্তি যদি সালিশী পরিষদের সিদ্ধান্ত না মানে তাহলে ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ আইনের ৪(গ) ধারার অধীনে একজন মুসলিম স্ত্রী তার ভরণপোষণ আদায়ের জন্য সরাসরি পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন।
স্ত্রীর ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইনের সীমাবদ্ধতা: মুসলিম আইন অনুসারে বিবাহের পর স্ত্রীকে ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর। অর্থাৎ স্ত্রী আর্থিকভাবে স্বামীর উপর নির্ভরশীল। এই বিধান বৈষম্যমূলক। কারণ উর্পাজন শুধু স্বামী করে না স্ত্রীও প্রত্যক্ষভাবে সংসারে দায়িত্ব পালন করে। সন্তান লালন-পালন, সংসার ব্যবস্থাপনার সকল দায়িত্ব নারীর উপর অর্পিত। অথচ স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ করবে – এই বক্তব্য পরিবারে নারীর ভূমিকাকে অস্বীকার করে। পরিবারে উর্পাজনশীল ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রী দুজনই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল।আইনের এই ভাষ্যে তা প্রকাশ পায়নি।
বিচ্ছেদকালীন ও বিচ্ছেদের পর ভরণপোষণ:
মুসলিম আইনে বিবাহ একটি চুক্তি। যেকোন চুক্তি দুইজন সমমর্যাদা সম্পন্ন মানুষের মধ্যে সম্পন্ন হয়। যেহেতু স্বামীর উপর স্ত্রী নির্ভরশীল সেজন্য এই আইনে সমমর্যাদার বিষয়টি উপেক্ষিত। ফলে দেখা যায় যে বিবাহ-বিচ্ছেদে স্বামীর একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকার ফলে আইনানুযায়ী স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে মাত্র নব্বই দিনের ভরণপোষণ পাবে। অথচ ঐ পরিবার গঠনে নারীর যে ভূমিকা সেই ভূমিকার কোন স্বীকৃতি আর থাকে না। নারী শুধু নব্বই দিন বা সন্তান সম্ভবা হলে শুধুমাত্র ইদ্দকালীন সময়ে ভরণপোষণ পাবে।
আবার বিবাহ-বিচ্ছেদের পর একজন নারী সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় যে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে সেই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির পথ কি? এখানে পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের দায় কি? রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এই দায় রাষ্ট্রকে নিতে হবে, বিবাহকালীন সময়ে পরিবারে অর্জিত সম্পত্তির উপর নারীর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরিবার ওসমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে যেখানে নারী তার স্বাধীন ও স্বকীয় মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে।
সন্তানের ভরণপোষণ: সন্তানের ভরণপোষণ করার দায়িত্ব আইনগতভাবে বাবার। সাবালক না হওয়া পর্যন্ত ছেলেকে এবং বিয়ের আগ পর্যন্ত মেয়েকে বাবা ভরণপোষণ দিবেন। অসুস্থ ও অক্ষম সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বাবার। সাবালকত্ব অর্জনের পরও যদি সন্তানরা নিজে উর্পাজন করতে অক্ষম হয় তাহলে বাবার কাছ থেকে সন্তান ভরণপোষণ পাবে। মা যখন সন্তানের জিম্মাদার তখনও স্বামী সন্তানের ভরণপোষণ করবেন।
অভিভাবকত্ব এবং জিম্মাদারিত্ব
১৮৯০ সালের অভিভাবক ও প্রতিপালন আইনের ৪(২) ধারা অনুসারে অভিভাবক বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যে ব্যক্তি কোনো নাবালকের শরীর অথবা সম্পত্তি অথবা শরীর ও সম্পত্তির উভয়ের তত্ত্বাধানের জন্য নিযুক্ত হন। সুতারাং অভিভাবকত্ব হলো নাবালক ও অভিভাবকের মধ্যকার সম্পর্ক, যা দ্বারা অভিভাবক নাবালকের শরীর ওসম্পত্তি দেখাশোনা করার অধিকার প্রাপ্ত হন।
আর জিম্মাদরিত্ব বলতে একটি নিদিষ্ট বয়স পর্যন্ত সন্তাানের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ, সার্বক্ষনিক দেখাশোনা এবং যতœ করার অধিকারকে বোঝায়। মুসলিম আইনে বাবা সন্তানের প্রকৃত আইনগত অভিভাবক। মুসলিম আইনে মা সন্তানের অভিভাবক হতে পারেন না। তবে মা সাত বৎসর পর্যন্ত ছেলে সন্তানকে ও বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে সন্তানকে কাছে রাখতে পারবেন। এই অধিকারকে বলে ‘হিজানা’ বা জিম্মাদারিত্ব।
মুসলিম আইন অনুযায়ী মা যদিও সন্তানের অভিভাবক নন, তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে মা আদালতে সন্তানের অভিভাবকত্বের জন্য আদালতে আবেদন করতে পারেন। যেমন – সন্তানের প্রকৃত অভিভাবক যিনি তিনি যদি সন্তানকে ঠিকমত দেখাশোনা না করেন বা সন্তানের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ বা সন্তানের কল্যাণে আগ্রহী নয় এরূপ ক্ষেত্রে মা নিজ সন্তানের কল্যাণার্থে তার কাছে সন্তান থাকা উচিৎ – এই মর্মেআদালতে আবেদন করতে পারবেন।
এই আইনের সীমাবদ্ধতা: এই আইনে মা ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে সাত বৎসর পর্যন্ত এবং মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে বয়:সন্ধিকাল পর্যন্ত মা জিম্মদার থাকতে পারবেন। এই আইন অনুযায়ি মা অভিভাবক হতে পারবেন না। তবে আদালতের আদেশ বলে মা সন্তানের উল্লেখিত বয়সের পরও জিম্মদার থাকতে পারবেন। যেখানের প্রাকৃতিকভাবেই মা-বাবা দুইজনই সন্তানের অভিভাবক হওয়ার কথা সেখানে মা অভিভাবক হতে পারবে না। সন্তানের জন্য সর্বাধিক শ্রম ও দায়িত্ব পালনে মা ভূমিকাই মূখ্য।
পিতৃহীন সন্তান বা পিতা যখন সন্তানকে ফেলে রেখে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রাধাণ্য দেন তখন সন্তানের একমাত্র অবলম্বন মা। মা সমস্ত দায়িত্ব ও ত্যাগ শিকার করে তিল তিল শ্রম দিয়ে সন্তানকে লালন-পালন করেও সেই সন্তানের অভিভাবকত্ব রাষ্ট্রীয় আইনে মা পাবেন না।এই ধরণের বৈষম্যমূলক আইন এখনো করে টিকে আছে। যদিও নাম কাওয়াস্তে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার নাম উল্লেখ করার বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু মূল আইনের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি।
পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫
১৯৮৫ সালে রাষ্ট্রপতির ১৮ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে পারিবারিক আদালত গঠন হয়। পার্বত্য রাঙ্গামাটি, পার্বত্য বান্দরবন এবং পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলা ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে এই আইন প্রযোজ্য হবে।
পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার: ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে পারিবারিক আদালতের পাঁচটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বা ঐ বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত বিষষের মামলা গ্রহণ, বিচার এবং নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার থাকবে এই আদালতের। পারিবারিক আদালতের বিষয়সমুহ হলো- ১. বিবাহ- বিচ্ছেদ, ২. দাম্পত্য সম্পর্ক পুরুদ্ধার, ৩. দেনমোহর ৪.ভরণপোষণ এবং ৫. অভিভাবকত্ব
মামলা কোথায় হবে: স্থানীয় সীমার আওতায় পারিবারিক আদালতে আরজি দাখিল করতে হবে। বিবাহ – বিচ্ছেদ, দেনমোহর এবং ভরণপোষণের মামলায় স্ত্রী বসবাস করে এরূপ স্থানীয় সীমায় অবস্থিত পারিবারিক আদালতে আরজি পেশ করতে হবে।
মুসলিম উত্তরাধিকার আইন
কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তার জীবিত আতœীয়-স্বজনদের যে অধিকার জন্মায় তাকে উত্তরাধিকার বলে।মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের মূল উৎস কুরাআন হলেও বিভিন্ন সময়ে মুসলিম আইন বিশারদগন তাদের অভিজ্ঞতার আলোক উত্তরাধিকার নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের ৩টি বৈশিষ্ট্য নি¤œরূপ-
১. জীবিত অবস্থায় যে কোন ব্যক্তির সম্পত্তিতে অন্য কারোর অধিকার জন্মায় না
২. যে কোন মুসলমান ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় তার সম্পত্তি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে
৩. কোন মুসলমান জীবিত অবস্থাতেই তার সম্পত্তি হস্তান্তর সম্বন্ধে নির্দেশ রেখে যেতে পারে যা তার মৃত্যুর পর কার্যকরি হয়। তাকে উইল বা অছিয়তনামা বলে।
উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের পূর্বশর্ত: একজন মুসলিম নারী বা পুরুষের মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টনের আগে নি¤œবর্ণিত শর্তসমূহ পালন করতে হবে
১. মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের খরচ পরিশোধ করা, ২. স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ করা, ৩. মৃত ব্যক্তির কোনো ঋণ বা দেনা থাকলে তা পরিশোধ করা, ৪. মৃত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো উইল করা থাকলে সেই উইলে উল্লেখিত সম্পত্তি প্রদান করা। এরপর যে সম্পত্তি থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন হবে।
মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীর সম্পত্তির অধিকার:মুসলি আইনের বিধানমতে উত্তরাধিকারীদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়- অংশীদার, অবশিষ্টভোগী, দুরবর্তী আত্মীয়। অংশীদারদের সম্পত্তি দেয়ার কিছু কিছু ব্যতিক্রম সাপেক্ষে অবশিষ্টভোগীরা সম্পত্তিতে অংশীদার হন। আর মৃত ব্যক্তির অংশীদার ও অবশিষ্ট ভোগী অংশীদার না থাকলে দুরবর্তী আত্মীয়গণ সম্পত্তি পান।
অংশীদারঃ মোট বারোজন অংশীদার। তার মধ্যে আটজনই নারী । এর মধ্যে পাঁচজন প্রধান অংশীদার। এই পাঁচজন অংশীদার হলো (ক) পিতা (খ) মাতা (গ) স্ত্রী/স্বামী (ঘ) ছেলে (ঙ) মেয়ে। প্রধানত এই পাঁচজন উত্তরাধিকারীর মাঝে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টন হয়ে থাকে। এই পাঁচজন উত্তরাধিকারী বেঁচে থাকলে বাকীরা সম্পত্তি পায় না।
মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীর সম্পত্তি:
কন্যা হিসাবে
- মৃত ব্যক্তির যদি একটি মাত্র কন্যা থাকে এবং কোন পুত্র না থাকে তাহলে কন্যা পিতার মোট সম্পত্তির অর্ধেক বা ১/২ অংশ পাবে
- মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান না না থাকে এবং দুই বা ততোধিক কন্যা থাকে তবে তারা সম্মিলিতভাবে মোট সম্পত্তির২/৩পাবে।
- মৃত ব্যক্তির কন্যার সাথে পুত্র থাকলে প্রত্যেক পুত্র কন্যার দ্বিগুন সম্পত্তি পাবে
স্ত্রী হিসাবে
- স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী দুইভাবে অংশ পান। প্রথমত যদি তাদের কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান না থাকে তাহলে স্ত্রী স্বামীর মোট সম্পত্তির ১/৪ অংশ পাবেন। দ্বিতীয়ত সন্তান থাকলে স্ত্রী মোট সম্পত্তির ১/৮ অংশ পাবেন। আবার যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকে তাহলে তারা ১/৪ অথবা ১/৮ অংশ নিজেদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে নেবেন।
- স্বামীও স্ত্রীর সম্পত্তিতে দুইভাবে অংশ পান। প্রথমত যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে তবে স্বামী স্ত্রীর মোট সম্পত্তির ১/২ অংশ পাবেন। দ্বিতীয়ত যদি স্ত্রীর সন্তান থাকে তা ওই স্বামীরই হোক বা অন্য স্বামীরই বা তাদের সন্তান থাকে তবে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির ১/৪ অংশ পাবে
মা হিসাবে
- মৃত্য ব্যক্তির কোনো সন্তান বা পুত্রের সন্তান থাকলে মা মোট সম্পত্তির ১/৬ অংশ পাবে
- যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান বা পুত্রের সন্তান না থাকে একজনের বেশি ভা ইবা বোন না থাকে তাহলে মা মোট সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবে
বোন হিসাবে - মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী কেউ না থাকলে এবং শুধু একজন বোন থাকলে বোন অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।
- মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র.পিতা, দাদা বেঁচে থাকলে বোন কোন সম্পত্তি পাবে না।
এখানে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কন্যা, স্ত্রী, মাতা ও বোন কেউই পিতা, স্বামী, ভাইয়ের সমান সম্পত্তি পায় না। আইনগতভাবে মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক সম্পত্তি পায়। আইনগত এই অধিকার থেকেও মেয়েদের বঞ্চিত করা হয়। আবার সমাজে এমন ধারণা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যে, যেসকল মেয়েরা সম্পত্তির অংশে নেয় তারা সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে নিচু স্তরের। মিথ্যা এই অভিজাত্যের কারণে বোনের সম্পত্তি সাধারণত ভাইয়েদের ভোগ দখলে চলে যায়। মাতাও ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তার সম্পত্তি ভাগের প্রশ্ন তোলেন না। - এই কথাও প্রচলিত আছে যে মেয়েরা বাবার কাছ সম্পত্তি পান আবার স্বামীর কাছ থেকেও সম্পত্তি পান। ফলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি সম্পত্তি পান। কিন্তু উল্লেখিত আলোচনাই দেখা গেল যে কোন অবস্থায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি সম্পত্তি পান না। সর্বক্ষেত্রে নারীর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যখন পৃথিবীব্যাপী তোলপাড় তখন আমরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই করছি।
- বর্তমান সরকার ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়ন নীতিমালার সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে বলেছিল – উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ ও ভূমির উপর অধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ দেয়া হবে। অথচ ২০১১ সালের নারী উন্নয়ন নীতিমালায় উপার্জনের, উত্তরাধিকার,ঋণ,ও ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানের কথা বলা হল। কোথায় সমান অধিকার আর কোথায় অর্জিত সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।
- একই সরকার দুই আমলে দুই ধরণের বক্তব্য প্রদান করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে নারীর সমমর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে। আর মুক্তিযুদ্ধের ধারক বাহক এই সরকার সংবিধান স্বীকৃত যে মৌলিক অধিকার তাকেও বাস্তাবায়ন করতে পারছে না। সংবিধানের মোলিক অধিকারের ২৮(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সরকার আর একটি প্রতারণা করছে তা হলো সিডও সনদের অসম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।
- সরকার আর একটি প্রতারণা করছে তা হলো সিডও সনদের অনুচ্ছেদকে সংরক্ষণ রেখে যেখানে পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনে বৈষম্য বিলোপের কথা বলা হয়েছে। নারী যখন পরিবার, সমাজ রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তখন উত্তরাধিকার আইনের এই বৈষম্য বিলোপ না করা নারীর প্রতি রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বিলোপ করে সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করাই হবে নারীর প্রতি রাষ্ট্রের যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।
এতিম নাতি-নাতনীদের সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকার
১৯৬১ সালের পূর্বে প্রচলিত আইন অনুসারে এতিম নাতি নাতনীরা তাদের নানা, নানী, দাদা বা দাদীর নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পত্তি পেত না। ‘মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ’ ১৯৬১ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে বলবৎ হয়েছে এবং এখনও এই আইন বাংলাদেশে বলবৎ রয়েছে।
১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৪ ধারার মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, যার সম্পত্তি বন্টন হবে তার মৃত্যুর পূর্বে তার কোন পুত্র বা কন্যা মারা গিয়ে থাকলে এবং মৃত পুত্র/ কন্যা সন্তান জীবিত থাকলে সম্পত্তি বন্টনের সময় তার সম্পত্তির ঐ অংশ পাবে, যা তাদের পিতা কিংবা মাতা বেঁচে থাকলে পেত। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির এতিম নাতি নাতনী থাকলে সম্পত্তি বন্টনের সময় তাদের বাবা মাকে জীবিত মনে করে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পূর্বে মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ তাদের পিতা মাতার স্থলাভিষিক্ত হবে, কিন্তু তাদের স্বামী বা স্ত্রী কিছুই পাবে না।
হিন্দু পারিবারিক আইন
হিন্দু আইন মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত আইন। হিন্দুদের বিবাহ, উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ, দত্তক গ্রহণ, অভিভাবকত্ব নির্ণয়, পারিবারিক সম্পর্ক নির্ধারণ ইত্যাদি হিন্দু পারিবারিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন,শিখ ও সাঁওতালদের ক্ষেত্রে এই আইন অনেকাংশে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত শ্রীলংকার একাংশে হিন্দু আইন প্রচলিত।
হিন্দু আইনের উৎস মূলত দু‘ভাগে বিভক্ত- ক. মিতক্ষরা, খ. দায়ভাগা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মিতক্ষরা আইন প্রচলিত থাকলেও মূলত বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ বাঙালি হিন্দুদের জন্য দায়ভাগা আইন প্রচলিত। বাংলাদেশে যেহেতু দায়ভাগা আইন প্রচলিত সেহেতু তার আলোকে হিন্দু পারিবারিক আইন আলোচনা করা হবে।
হিন্দু আইনে বিবাহ
হিন্দু আইনে বিবাহ কোন চুক্তি নয়। এটি একটি ধর্মীয় সংস্কার এবং নারী-পুরুষের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। হিন্দু বিয়ের শর্তসমুহ নি¤œরূপ
ক. বয়স :১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ফলেহিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে বর ও কনের সর্বনি¤œ বয়সযথাক্রমে মেয়ের১৮ বছর ও ছেলের২১ বছর।
খ.সম্মতি: বিবাহে বর ও কনের স্বেচ্ছা সম্মতি থাকতে হবে। জোড়পূর্বক বিবাহ কোনো বিবাহ হলে বর বা কনে যেকোন পক্ষ বিবাহ বাতিলের জন্য দেওয়ানি আদালতে ঘোষণামূলক মোকাদ্দমা করতে পারবে।
গ. আচার-অনুষ্ঠান:
১. যজ্ঞ বা কুশ-িকা: যজ্ঞ একটি অনুষ্ঠান- যেখানে শাস্ত্র মতে বেদমন্ত্র পাঠ করা হয় এবং পুরোহিতের বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান করা হয়।
২. সপ্তপদী বা সাতপাকে ঘোরা : বিবাহ অনুষ্ঠানে আগুনের চারদিকে বর ও কনের একসাথে সাতপাক ঘোরা বা সাত পদক্ষেপ অতিক্রম করাকে সপ্তপদী বলে।
হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২
হিন্দু বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার লক্ষ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনকে ঐচ্ছিক রেখে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে“হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২“ পাশ হয়। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক হিন্দু নারী-পুরুষ শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ি বিবাহ করার পর বিয়ের দালিলিক প্রমাণের উদ্দেশে নির্দিষ্ট ফি নিবন্ধকের নিকট জমা দিয়ে বিবাহ নিবন্ধন ও বিবাহ নিবন্ধনের প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে পারবে। এই লক্ষে প্রতিটি সিটি করর্পোরেশন এলাকায় একজন নিবন্ধক নিয়োগ ও তার এলাকা নির্দিষ্ট করা এবং উপজেলা পর্যায়ে একজন ব্যক্তিকে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হবে। বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নাগরিকের জন্য এই আইন প্রযোজ্য।
হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন ঐচ্ছিক হওয়ার কারণে পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু নারীরা বিবাহ নিবন্ধন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে নারীরা বিবাহে অস্বীকৃতি ও প্রতারণার শিকার হবে। এছাড়া এই আইনটি শুধু হিন্দু ধর্মালম্বীদের জন্য হওয়ার কারণে বৌদ্ধসহ অন্যান্য ধর্মাললম্বীরা যারা হিন্দু আইন অনুসরণ করে তারা বিবাহ নিবন্ধন থেকে বঞ্চিত হবে।
বিধবা বিবাহ :
১৮৫৬ সালে ‘হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন’ পাস হওয়ার ফলে বিধবা বিবাহ এখন আইনসস্মত। ১৮৫৬ সালের হিন্দু বিধবা বিবাহ আইনের উল্লেখ্য বিষয়সমুহ হলো-
১. হিন্দু বিধবাদের বিবাহ বৈধকরণ: কোনো বিবাহিত হিন্দু নারীর যদি স্বামী মারা যায় তাহলে উক্ত নারী পুনরায় বিয়ে করতে পারবেন এবং এই বিয়ের ফলে যদি কোনো সন্তান জন্ম লাভ করে তবে সে সন্তান বৈধ সন্তান বলে বিবেচিত হবে।
২. পুনর্বিবাহের কারণে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার বিলুপ্তি : বিধবার পুনরায় বিয়ে হলে তিনি তার পূর্ব স্বামীর দিক থেকে আইনের দৃষ্টিতে মৃত বলে গণ্য হয় এবং সে কারণে পুনর্বিবাহের ফলে তার প্রাক্তন স্বামীর সম্পত্তির ওপর থেকে তিনি অধিকার হারান।
৩. বৈধ বিবাহের প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদি বিধবা বিয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য: সাধারণত বিয়ের ক্ষেত্রে যেসব অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয় বিধবা বিয়ের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।
৪. সম্মতি: বিধবা বিয়ের ক্ষেত্রে বিধবার সম্মতি অবশ্যই নিতে হবে
শাস্তি: ১৮৫৬ সালের বিধবা বিয়ের এই আইন ভঙ্গ করলে ১ বছর কারাদ- বা জরিমানা বা উভয় দ-ে দ-িত হতে পারেন।
হিন্দু আইনে পৃথক বাস
বাংলাদেশেরহিন্দু আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু আইনে বিবাদমান দম্পতি বড় জোর ‘বিবাহিত নারীর পৃথক বাসস্থান ও ভরণপোষণ আইন১৯৪৬’ অধীনে আদালতে মামলা দায়ের করলে আদালতের রায় সাপেক্ষে একে অপরের থেকে পৃথক বসবাস করতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থেকেও স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবে।
আদালত স্বামী স্ত্রীর সামাজিক অবস্থা, স্বামীর সামর্থ্য এবং স্ত্রীর দাবির পরিমাণ, সার্বিক অবস্থা এবং স্ত্রী বিবাহের পূর্বে তার বাবার গৃহে যেভাবে জীবন যাপন করতো তার উপর ভিত্তি করে বা বিবেচনা করে ভরণপোষণ নির্ধারণ করে থাকে। উল্লেখ্য যে পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে ১৯৫৫ সালে ‘হিন্দু বিবাহ আইন’পাশ হওয়ার ফলে স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই আদালতে সুনির্দিষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত কারণ উপস্থাপনের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন।
হিন্দু আইনে ভরণপোষণ:
ভরণপোষণ বলতে পরিবারের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করাকে বুঝায়। হিন্দু আইন অনযায়ী সম্পত্তি না থাকলেও একজন হিন্দু পুরুষ তার নাবালক পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, পিতামাতার ভরণপোষণ করতে বাধ্য। এছাড়া কর্তা যৌথ পরিবারের সকল পুরুষ, তাদের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের ভরণপোষণ করতে আইনত বাধ্য।
১. পুত্র: নাবালক পুত্রের ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু পুত্র সাবালক হলে এ দায়িত্ব আর পিতার থাকে না।
২. অবিবাহিত কন্যা- কন্যার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তার ভরণপোষণ করা আইনত ও নীতিগত ভাবে পিতা বাধ্য। কন্যা সাবালিকা হলেও এ দায়িত্ব থাকে। পিতার মৃত্যুর পরও পিতার সম্পত্তি থেকে কন্যা এই ভরণপোষণ পাবে। কোন কন্যা নি:সন্তান অবস্থায় বিধবা হলে এবং তার স্বামীর সম্পত্তি থেকে ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা না থাকলে বাবা নীতিগতভাবে ঐ কন্যারও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবেন।
৩. স্ত্রী: ভরণপোষণ দেয়ার সঙ্গতি থাক বা না থাক হিন্দু স্বামী তার স্ত্রীর ভরণপোষণ অবশ্যই দেবেন
৪. বিধবা: হিন্দু বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভ না করলেও আজীবন ভরপোষণ পাওয়ার অধিকারী।
৫. অযোগ্য উত্তরাধিকারী: অক্ষমতা ও অযোগ্যতার কারণে কোন অংশীদার পৈতিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলেও তারা অবশ্যই ভরণপোষণ পাবে। যে বা যারা উত্তরাধিকার লাভ করবে তাদের দায়িত্ব হবে অক্ষমদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা।
৬. ‘বিবাহিত নারীর পৃথক বাসস্থান ও ভরণপোষন আইন ১৯৪৬’ অনুয়ায়ি যেসব ক্ষেত্রে একজন বিবাহিত নারী তার স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থেকেও ভরণপোষণ পাবেন, তাহল –
১. স্বামী যদি কোন দূরারোগ্য বা যৌনব্যাধিতে দীর্ঘকাল আক্রান্ত থাকে
২. স্বামী যদি তার স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে
৩. স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সন্দেহ করে
৪. স্বামী যদি অন্য ধর্ম গ্রহণ করে
৫. স্ত্রী থাকা অবস্থায় স্বামী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করে
৬. স্বামী যদি বিবাহ বর্হিভূত কোন সম্পর্ক রাখে
৭. স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামী যদি পলাতক থাকে
হিন্দু আইনে নাবালকত্ব ও অভিভাবকত্ব:
১৮৭৫ সালে ‘সাবালকত্ব আইন পাশ হওয়ার ফলে কোন ব্যক্তির বয়স ১৮ হলে তাকে সাবালক বলা হয়। এই আইন বাংলাদেশে প্রযোজ্য।হিন্দু আইনে অভিভাবক তিন ভাবে হতে পারে –
১. স্বাভাবিক অভিভাবক, ২. বাবা কর্তৃক উইল দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবক এবং ৩. আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক
স্বাভাবিক অভিভাবক বলতে বাবাকে বুঝায়। বাবার মৃত্যু হলে সাধারণভাবে মা নাবালকের ও তার সম্পত্তির আইনগত অভিভাবক হন। কিন্তু বাবা জীবদ্দশায় উইল করে অন্য কোন ব্যক্তিকে নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত করে গেলে মার অভিভাবকত্ব দুরূহ হয়ে পড়ে। আবার যদি কোন নাবালকের বাবা মা কেউ না থাকে তবে আদালত নিকটবর্তী আত্মীয়দের মধ্যে থেকে একজনকে নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত করবেন।
দত্তক গ্রহণ :
অন্য কোন ব্যক্তির পুত্র সন্তানকে হিন্দু আইনের বিধান অনুযায়ি নিজ পুত্র রূপে গ্রহণ করাকে দত্তক বলে। বর্তমানে হিন্দু আইন ব্যতিত অন্য কোন আইনে দত্তক গ্রহণের বিধান নেই।
দত্তক গ্রহণের যোগ্যতা:
১. দত্তক গ্রহণকারিকে অবশ্যই আইনগতভাবে দত্তক গ্রহণের উপযুক্ত হতে হবে। দত্তক গ্রহণকারিকে একজন সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারি পুরুষ হতে হবে।
২. দত্তক যিনি গ্রহণ করবেন তার কোন পুত্র, পৌত্র অথবা প্রপৌত্র থাকলে দত্তক নিতে পারবেন না।
৩. একজন অবিাহিত অথবা বিপতœীক পুরুষও দত্তক গ্রহণ করতে পারবে
হিন্দু নারীর দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা:
১. অবিবাহিত নারী- বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কোন অবিবাহিত হিন্দু নারী দত্তক নিতে পারেন না।
২. বিবাহিত নারী: বিবাহিত স্ত্রী স্বামীর জীবদ্দশায় স্বামীর অনুমতিক্রমে স্বামীর জন্য দত্তক গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু নিজের জন্য দত্তক গ্রহণ করতে পারবেন না।
৩. বিধবা নারী: স্বামীর জীবদ্দশায় স্বামীর অনুমতি দিলে একজন বিবধা স্বামীর জন্য দত্তক নিতে পারেন।
দত্তক দাতার যোগ্যতা:
আইন অনুসারে শুধুমাত্র বাবা-মা ই দত্তক দেয়ার অধিকারি। তবে মা বাবার অনুমতি ছাড়া সন্তানকে দত্তক দিতে পারেন না। বাবা সংসার ত্যাগী বা মস্তিষ্কবিকৃত জনিত অসুস্থতার কারণে অক্ষম হলে বাবার আপত্তি না থাকলে মা দত্তক দিতে পারেন। এ অধিকার কারও উপর অর্পন করা যায় না। তাই বাবা-মা নেই এমন কাউকে দত্তক নেয়া যায় না কারণ তাকে দত্তক দিতে পারে আইনগতভাবে এমন কেউ নেই।
কাকে আইনত দত্তক নেয়া যায় :আইনের শর্ত অনুযায়ি একই বর্ণের ছেলে সন্তানকে দত্তক নিতে হবে।
হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর সম্পত্তি
বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার আইন দায়ভাগা আইনমতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এখানে আমরা উত্তরাধিকার আইনে হিন্দু নারীদের অবস্থান দেখবো।
দায়ভাগা আইনমতে উত্তরাধিকারদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়-
১. সপিন্ড -(মোট ৫৩ জন) এরা প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী।
২. সকুল্য -(মোট ৩৩ জন) এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী। এবং
৩. সমানোদক-(মোট ১৪৭ জন) এরা তৃতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী।
মৃত ব্যক্তির মোট উত্তরাধিকারীর সংখ্যা (৫৩+৩৩+১৪৭) = ২৩৩ জন।
উক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে সপি-রা কেউ থাকলে সকুল্যরা সম্পত্তি পাবে না , আবার সকুল্যরা থাকলে সমানোদকরা সম্পত্তি পাবেনা। এক্ষেত্রে সপি-দের সংখ্যা ৫৩ জন, ফলে সকুল্য ও সমানোদকরা সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই সপি-দের আলোচনায় এখানে প্রধান বিবেচ্য। সপি- ৫৩ জনের মধ্যে নারী মাত্র পাঁচ জন, এরা হলেন-বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী।
সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন ১৯৩৭ পাশ হওয়ার পর বিধবা এক বা একাধিক হলে সকলে মিলে এক পুত্রের সমান সম্পত্তি জীবনসত্বে ভোগ দখল করতে পারবেন। স্ত্রীর পরেই কন্যার দাবি। কন্যাদের মধ্যে প্রথমে অবিবাহিত কন্যা, এরপর ছেলে সন্তান আছে এমন কন্যারাই জীবনসত্বে সম্পত্তি লাভ করবেন। যে সকল কন্যাদের সম্পত্তি নেই, যে সকল বিধবা কন্যাদের পুত্র সন্তান নেই, যে কন্যাদের শুধুমাত্র কন্যা সন্তান তারা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। এই আলোচনায় দেখা যায় হিন্দু নারীরা উত্তরাধিকার সূত্রে কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্পত্তি পেলেও তা শুধু ভোগ করতে পারবেন কিন্তু বিক্রি, উইল দান, স্বাধীনভাবে হস্তান্তর ইত্যাদি করতে পারেন না। শুধু মাত্র তিনি যার কাছ থেকে সম্পত্তি পেয়েছেন তার শ্রাদ্ধ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন।
স্ত্রীধন
স্ত্রীধন হল যে সম্পত্তিতে একজন নারীর পূর্ণ মালিকানা বা অধিকার রয়েছে অর্থাৎ যেসব সম্পত্তি নারীরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিক্রি, উইল, মালিকানা পরিবর্তন এবং ভোগদখল করতে পারে। এক কথায় যেসব সম্পত্তিতে নারীরা সম্পূর্ণ স্বত্বের অধিকারী হয় সেই সব সম্পত্তিকেই স্ত্রীধন বলা হয়। স্ত্রীধন আলোচনার ক্ষেত্রে স্ত্রী বলতে কারো বিবাহিত, মেয়ে বা যে কোন নারীকে বোঝানো হয়েছে।
স্ত্রীধন মালিকানা প্রাপ্তির উপায়সমূহ
একজন নারী যে সমস্ত উপায়ে স্ত্রীধনের মালিকানা প্রাপ্ত হয় তা নি¤েœ দেয়া হলো: যথা-
১. একজন নারী কুমারী, বিবাহিত অথবা বিধবা অবস্থায় উত্তরাধিকারসূত্র ব্যতীত অন্য যেকোনভাবে সম্পত্তির মালিক হলে সেই সব সম্পত্তিই স্ত্রীধন।
২. স্বামী-স্ত্রী পৃথক বসবাস থাকা অবস্থায় স্বামীর নিকট থেকে ভরণপোষণের জন্য প্রাপ্ত মাসোহারা দ্বারা অর্জিত সম্পত্তিও স্ত্রীধন হিসেবে গণ্য হবে।
৩. স্ত্রীধন দ্বারা অর্জিত সম্পত্তিও স্ত্রীধন।
উল্লেখিত উপায়ে প্রাপ্ত সম্পত্তি একজন নারী ইচ্ছানুযায়ী ভোগ, দখল, বিক্রি, উইল, দান ইত্যাদি করতে পারবেন। এছাড়া কোন নারী নিজে উর্পাজন করে সম্পত্তি অর্জন করলে তা স্ত্রীধন হিসাবে গণ্য হবে।
হিন্দু আইনের সংস্কার:
স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরেও এদেশে নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে একথা চরম-পরম সত্য । উল্লেখিত বিবাহ, পৃথকবাস, ভরণপোষণ, দত্তক গ্রহণ, উত্তরাধিকার আইন এই আইনগুলোর প্রত্যেকটিতে নারীর অধিকার চরমভাবে লংঘিত। বিবাহের রেজিস্ট্রেশণ প্রথা বাধ্যতামূলক নয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার নেই। একজন হিন্দু নারী শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হলেও তার কোন পথ নেই বিবাহ-বিচ্ছেদের।
আধুনিক এই সভ্য যুগে এই ধরণের আইন এখনো বহাল আছে। দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে আরো খর্ব করা হয়েছে। একমাত্র স্বামীর জন্য একজন নারী দত্তক গ্রহণ করবে। একইভাবে সম্পত্তি শুধু পুত্র সন্তানের অধিকারে থাকবে। নারীর সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব থাকলে তা শুধু ভোগদখলের জন্য। কারণ পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্জা- এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করাই হিন্দু আইনের মূল লক্ষ। অথচ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের হিন্দু পারিবারিক আইনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।
যেমন-হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫, নাবালকের সম্পত্তি বিষয়ক আইন ১৯৫৬, হিন্দু দত্তক গ্রহণ ও ভরণপোষণ আইন ১৯৫৬, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৯৫৬। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইনেএখনো সেই রক্ষণশীল প্রাচীন ধ্যানধারণাই রয়ে গেছে। হিন্দু পারিবারিক আইন পুরোপুরি নারী অধিকারের পরিপন্থী। তাইহিন্দু পারবারিক আইনের সংস্কার এখন সময়ের দাবি।
খ্রিস্ট্রান পারিবারিক আইন
খিস্ট্রান ধর্মাবলম্বীরা মূলত দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত-ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। বাংলদেশের খিস্ট্রানদের মধ্যে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত জনসংখ্যাই বেশি। ক্যাথলিকদের পারিবারিক আইনের প্রধান গ্রন্থ হলো – ‘কোড অফ ক্যানন ল’। বিবাহ, বিবাহের বৈধতা, বিবাহ বাতিলকরণ ও সন্তানের বৈধতা ইত্যাদি বিষয় ‘কোড অফ ক্যানন ল’ উল্লেখ করা আছে।
আর সনাতন রোমান ক্যাথলিক চার্চের সাথে বিরোধের ফলে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভব। প্রটেস্ট্যান্টরা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও পারিবারিক আইনে অনেক সংস্কার সাধন করেছেন, ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারিবারিক আইনের অনেক বিষয়ের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।
আমাদের দেশে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রচলিত আইনসমুহ হলো- ডিভোর্স অ্যাক্ট ১৮৬৯, খ্রিস্ট্রান ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৮৭২, গার্ডিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট ১৮৯০, ম্যারেড উইম্যানস প্রপারিটি অ্যাক্ট ১৮৭৪, সাকসেশন অ্যাক্ট ১৯২৫ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯। এই আইনগুলোর মধ্যে ডিভোর্স অ্যাক্ট ১৮৬৯, খ্রিস্ট্রান ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৮৭২ ও সাকসেশন অ্যাক্ট ১৯২৫ সাধারণত প্রটেস্ট্যান্টরা অনুসরণ করে।
খ্রিস্টান আইনে বিবাহ
বাংলাদেশে ক্যাথলিকদের বিয়ে সম্পাদিত হয় মূলত ‘কোড অফ কানন আইনে’। ক্যানন আইনের ১০৫৫ ধারায় বিয়েকে বলা হয়েছে, একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও একটি চুক্তি। আর ১০৫৬ ধারায় বিবাহের বৈশিষ্ট্য বলতে ঐক্য আর অবিচ্ছেদ্যতাকে বুঝানো হয়েছে। অন্যদিকে প্রটেস্ট্রান্ট খ্রিস্টানদের বিয়ে সম্পাদিত হয় খিস্ট্রান ম্যারেজ এ্যাক্ট ১৮৭২ এর অধীনে।
কিন্তু এই আইনের কোথাও বিয়ের সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। তবে ১৮৭২ সালের ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী লিখিতভাবে বিয়ে সম্পাদন করতে হবে এবং অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ক্যাথলিকদের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট চার্চে বিবাহ নিবন্ধন করতে হবে।
খ্রিস্টান বিয়ের শর্ত ঃ খ্রিস্টান ম্যারেজ এ্যাক্ট ১৮৭২ এর ৬০ ধারা অনুযায়ী খ্রিস্টান বিয়ের শর্তসমুহ নি¤œরূপ ঃ
১. বয়স ঃ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯, বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ বিবাহে ইচ্ছুক খ্রিস্টান ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ এবং মেয়ের বয়স কমপক্ষে ১৮ হতে হবে।
২. বৈবাহিক অবস্থা ঃ খ্রিস্টান ধর্মে বহুবিবাহ সম্পূর্ন নিষিদ্ধ। বিয়েতে বর বা কনে কারোরই আগের কোন স্বামী বা স্ত্রী বর্তমান থাকা চলবে না। কোন খ্রিস্টান পুরুষ বা নারী যদি তার স্ত্রী বা স্বামীর জীবদ্দশায় ও বিবাহ চলাকালে কাউকে বিয়ে করে তাহলে সেই ব্যক্তি আইনগতভাবে শাস্তি ভোগ করবেন।
৩.সাক্ষী ঃ খ্রিস্টান বিয়ে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে। সাক্ষীদের অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে।
৪.সম্মতি ঃ বিয়ের অনুষ্ঠানে বরও কনে উভয়কেই পরিস্কারভাবে বিয়েতে তাদের নিজ নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করতে হবে।
৫. রেজিস্ট্রেশন ঃ খ্রিস্টান বিয়ে রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক। প্রটেষ্টান্টরা তাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ম্যারেজ রেজিস্টারের কাছে। ক্যাথলিকগণ তাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করে চার্চের ধর্মযাজকের কাছে।
খ্রিস্ট্রান বিয়ের পদ্ধতি
ক. নোটিশ ঃ যে দু’জন নর-নারী বিয়ে করতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে যে কোন একজন চার্চের ধর্মযাজকের উদ্দেশ্যে একটি নোটিশ পাঠাবে এবং নোটিশের ফরমে অবশ্যই বর-কনের নাম, বয়স ও পেশা, দুজনের আবাসস্থল, কতদিন ধরে সেখানে বসবাস করছে, কোথায় বিয়ে সম্পন্ন হবে ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। এই নোটিশ পাওয়ার পর চার্চের ধর্মযাজক নোটিশটি খোলা জায়গায় লাগাবেন, যাতে তা সবার নজরে পড়ে।
খ. সার্টিফিকেট ঃ নোটিশ পাওয়ার কমপক্ষে চারদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেই চার্চের ধর্মযাজক একটি সার্টিফিকেট প্রদান করবেন এবং এর আগে বর-কনের কাছ থেকে একটা ঘোষণা নিবেন যে, ১. তাদের মধ্যে এমন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বা রক্তের সম্পর্ক নেই, যা বিয়েতে আইনগত বাধা হিসেবে কাজ করবে অথবা ২. তাদের বর্তমানে জীবিত কোন স্বামী/স্ত্রী নেই।
গ. বিয়ের অনুষ্ঠান ঃ বিয়ের সার্টিফিকেটের কার্যকারিতা দু’মাস পর্যন্ত থাকে। এ দু’মাসের মধ্যে বিয়ে সম্পাদিত হতে হবে।
খ্রিস্টান পারিবারিক আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ:
বাংলাদেশে খ্রিস্টান ধর্মালম্বীরা ডিভোর্স এ্যাক্ট ১৮৬৯ এর অধীনে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। তারা তিনটি উপায়ে বিবাহ বিচ্ছদ ঘটাতে পারে।
১. বিবাহ বিচ্ছেদ
২.বিবাহ বাতিল করণ
৩.জুডিসিয়াল সেপারেশন
বিবাহ বিচ্ছেদ: ১৮৬৯ সালের ডিভোর্স অ্যাক্ট এর ১০ ধারা মতে, স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনে স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে আবেদেন করতে পারেন। আবার স্ত্রী নি¤œলিখিত কারণে আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করতে পারে-
ক্স স্বামী যদি ধর্ম ত্যাগ করে অন্যধর্ম গ্রহণ করে এবং আরেকটি বিবাহ করে
ক্স কোন নিকট আতœীয় বা অন্যকারো সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকলে
ক্স ধর্ষণ, সমকামিতা, পাশবিকতা অথবা
ক্স যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া দু’বছরের বেশি সময ধরে স্ত্রীর খোঁজ – খবর না নিলে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে আবেদন করতে পারবেন।
তবে এই আইনে স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনে এবং তা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে স্বামী দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করে আদালতে মামলা করতে পারবেন। আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সে ব্যক্তিকে আদালত ক্ষতিপূরণ ও কিছু ক্ষেত্রে মামলার খরচ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে। পক্ষান্তরে একজন স্ত্রী যদি একইরকম অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে করেন এবং একইরকমভাবে কোনো নারীকেও যদি তার স্বামী ব্যভিচারে লিপ্ত থাকার অভিযোগ করে সেক্ষেত্রে স্ত্রী কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না।
বিবাহ বাতিল: যেকোন খ্রিস্টান নারী-পুরুষ নি¤েœাক্ত কারণে বিবাহ বাতিলের জন্য আদালতে আবেদন করতে পারেন। আদালত নি¤œলিখিত কারণগুলোতে বিয়ে বাতিল ঘোষণা করতে পারে
ক্স স্বামী যদি বিবাহের সময় এবং মামলা দায়ের করা অবধি পুরুষত্বহীন থাকে
ক্স যদি সম্পর্কের কারণে বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ হয়ে থাকে
ক্স বিবাহের সময় স্বামী/স্ত্রী যদি সুস্থ মস্তিষ্কের না থাকে কিংবা পাগল থাকে
ক্স স্বামী/স্ত্রী যেকারো পূর্বের বিবাহটি যদি আইনত কার্যকর থাকে
জুডিসিয়াল সেপারেশন: এই ব্যবস্থায় ব্যভিচার, নৃশংসতা বা কোন কারণ ছাড়া দু‘বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে স্বামী বা স্ত্রী যদি এক পক্ষকে পরিত্যাগ করে তবে ক্ষতিগ্রস্ত অপরপক্ষ আদালতে জুডিসিয়াল সেপারেশনের ডিক্রির জন্য আবেদন করতে পারেন। আদালত উল্লিখিত কারণগুলোর সত্যতা বিচার করে জুডিসিয়াল সেপারেশনের ডিক্রি জারি করতে পারেন।
খ্রিস্টান আইনে ভরণপোষণ:
ক্স খিস্টান আইনে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের পর এবং বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলাকালীন সময়ে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারি।
ক্স বিবাহ বিচ্ছেদ চলাকালীন সময়ে স্ত্রীর স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ দাবি করতে পারেন। তবে আদালত নির্ধারণ করবে এর পরিমাণ কি হবে। আদালত যে ভরণপোষণ নির্ধারণ করে দেবে তা স্বামীর বিগত তিন বছরের গড় আয়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগের বেশি হবে না।
ক্স বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও একজন খিস্ট্রান নারী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবেন তবে তা নির্ধারণ করে দেবে আদালত।
ক্স ব্যভিচার প্রমাণিত হয়েও যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তাহলে স্ত্রী আদালত কর্তক স্বামীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাবে এবং তার পরিমাণ বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রির সাথেই উল্লেখ থাকে । এই ভরণপোষণ মাসিক বা সাপ্তাহিক হতে পারে।
ক্স স্বামী যদি কোন কারণে অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম হয় তবে আদালত তাকে ভরণপোষণের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে পারে কিংবা পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে।
ক্স আর স্বামী যদি স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করে তবে একজন খিস্টান নারী বাংলাদেশের ফৌজদারি র্কাযবিধির ৪৮৮ ধারা অনুসারে আদালতে আবেদন করতে পারে।
সন্তানের ভরণপোষণ: সন্তানের ভরণপোষণ ও জিম্মাদরিত্বের বিষয়টি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হয়। তবে খ্রিস্টান ধর্মমতে পিতাই সস্তানের প্রকৃত অভিভাবক বিবেচিত হওয়ায় এর দায়িত্ব পিতার উপর বর্তায়।
খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনে নারী
বাংলাদেশের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উত্তরাধিকার নির্ধারণ হয় ১৯২৫ সালের সাকসেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী। কোন খ্রিস্টান নাগরিক মৃত্যু হলে তার সম্পত্তি সাকসেশন এ্যাক্টের ২৭ ধারায় নিয়মানুযায়ী ভাগ করা হয়। এই নিয়মগুলি উত্তরাধিকার নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য। নিয়মগুলো হল:-
১. উত্তরাধিকার হিসেবে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার।
২. পূর্ণরক্ত সর্ম্পক ও অর্ধ-রক্ত সর্ম্পকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই
৩. নিকটবর্তী আত্মীয় দুরবর্তী আত্মীয়কে প্রতিস্থাপিত করে
৪. মাতৃ-গর্ভের সন্তানও উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য হবে।
ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার জনগোষ্ঠির পারিবারিক আইন:
বাংলাদেশে মোট ১৫টির মতো ক্ষুদ্রজাতি সত্ত্বার অবস্থান রয়েছে। চাকমা/মগ/খুমী/ এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। সাঁওতাল/রাজবংশী/খাশিয়া/ গারো/হাজং/সিন্ধা/হাদি/পলিয়া/মনিপুরী/ত্রিপুরা/ এরা মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। পরে এদের কেউ কেউ খ্রিস্ট্রান ধমর্ও গ্রহণ করেছে। এই ক্ষুদ্রজাতি সত্ত্বাসমুহের ধরা বাধা পারিবারিক আইন নেই। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথা ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই তাদের পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিশাল জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজন লিখিত পারিবারিক আইন।
বিশেষ বিবাহ আইন ১৮৭২
মুসলিম, হিন্দু ও খিস্ট্রান প্রত্যেকে পারিবারিত আইন অনুযায়ি বিয়ে করতে পারে। তবে মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিস্টান এই তিনটি পারিবারিক আইনের বাইরেও বিবাহের জন্য একটি আইন আছে যা বিশেষ বিবাহ আইন নামে পরিচিত। এই আইনে বলা আছে, যে সকল ব্যক্তি খ্রিস্টান, ইহুদী, হিন্দু, মুসলিম, পারসি, বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈন কোনো ধর্মই পালন করে না সে এই আইনের অধীনে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু বিবাহটি যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, ও জৈন ধর্মাবল¤ী^ নারী ও পুরুষ মধ্যে হয় তবে তারা নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে।
বিশেষ বিবাহ আইনের শর্ত: বিশেষ বিবাহ আইনে বিয়ে করতে হলে ছেলে ও মেয়ে দু’জনকেই –
১. অবিবাহিত থাকতে হবে। অর্থাৎ তাদের অন্য কোনো স্বামী বা স্ত্রী বর্তমান থাকতে পারবে না
২. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের অধীনে ছেলের বয়স ২১ এবং মেয়ের বয়স ১৮ হতে হবে
৩. বিবাহের দু’পক্ষ পরস্পরের সাথে রক্ত সম্পর্ক বা রক্ত সম্পর্কীয় বা আত্মীয়তার কারণে নিষিদ্ধ স্তরের কেউ হতে পারবে না
রেজিস্ট্রেশন: বিয়ের যেকোন একপক্ষ রেজিস্টারের কাছে বিয়ের জন্য লিখিত নোটিশ পাঠাবে। এই বিয়ে সরকার নিয়োজিত একজন রেজিস্টার সম্পাদন করবেন। নোটিশ দেয়ার ১৪ দিন পর বিবাহ সম্পাদন করা হবে। এই বিবাহে কারো আপত্তি থাকলে দেওয়ানি আদালতের শরনাপন্ন হতে পারবে। এই বিয়েতে তিনজন সাক্ষী ও রেজিস্টার উপস্থিত থাকবেন।
উল্লেখ্যএই আইনের অধীনে যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তারা ১৮৬৯ সালের ডিভোর্স এ্যাক্টের অধীনে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে এবং সন্তানদের সম্পত্তি সাকসেশন অ্যাক্ট ১৯২৫ অনুয়ায়ি ভাগ করা হবে
সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের এই যুগে এসে আমাদেরকে নারী-পুরুষের সমতা তথা পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনে সমতার দাবি উত্থাপন করতে হচ্ছে। কারণ উল্লেখিত আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে -ধর্মভিত্তিক কোন পারিবারিক আইনেই নারী পুরুষের সমান অধিকার নেই। বিভিন্ন ধর্মীয় পারিবারিক আইনেবিবাহের শর্তে ভিন্নতা রয়েছে।
শর্ত সাপেক্ষে মুসলিম নারী বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারলেও হিন্দু ধর্মের নারীর বিবাহ বিচ্ছেেেদর অধিকার নেই। সন্তানের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে। মুসলিম ও খ্রিস্ট্রান পারিবারিক আইনে দত্তক নেয়ার বিধান নেই। হিন্দু আইনে দত্তক গ্রহনের বিধান থাকলেও সেখানে একমাত্র পুরুষের কর্তৃত্বই প্রধান। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তিতে নারীর অংশ বৈষম্যমূলক। কোনো বাবার যদি এক বা একাধিক কন্যা সন্তান থাকে তাহলে আইন অনুসারে বাবা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বে তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ কন্যা সন্তানকে দিতে পারবে না। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থান সবচেয়ে অবহেলিত।
এখানে নারীর নিজস্ব অর্জিত সম্পত্তি বা উপহার সামগ্রী ছাড়া এক কথায় স্ত্রী-ধন ব্যতিত আর কোন সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্ব নারী পায় না। তবে খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তিতে নারী পুরুষের অধিকার প্রায় সমান।
পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন সংস্কারে বাধা কোথাও। মুসলিম প্রধান দেশ তুরস্ক, তিউনিশিয়াসহ আরো কয়েকটি দেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হিন্দু প্রধান দেশ ভারতে ধর্মীয় প্রথার অধিকাংশই বাতিল ও সংস্কার করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে যখনই পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনে পরিবর্তনের প্রশ্ন আসে তখনই সাম্প্রদায়িক শক্তির দোহাই দিয়ে সরকার এই আইনের পরিবর্তনে কোন ভূমিকা পালন করে না।
বরং রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই সাম্প্রদালিক রাজনীতি ও শক্তিসমুহকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। কারণ সর্বক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার চেয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার হীন স্বার্থে সাম্প্রদায়িক – মৌলবাদী রাজনীতি ও শক্তিসমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা করাই তার লাভজনক ক্ষেত্র। সরকারের এই হীন স্বার্থইপ্রমাণ করে নারীর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি।
কেন পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জরুরী। কারণ আইনের এই বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর অধস্ত:ন অবস্থাকে বার বার স্মরণ করে দেয় নারী রাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সরকার নারীর অবদানের কথা পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী সমান হলেও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীর অংশগ্রহণ বেশি প্রায় ৫৩ শতাংশ।
চিকিৎসা ও আইনসহ অন্যান্য পেশাগত শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহন ৩৮ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন তথ্যমতে, সাড়ে ৬ লাখ নারী শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। এছাড়া বিজ্ঞানী, ব্যাংকার, গণমাধ্যম, সংস্কৃতি কর্মী, রাজনীতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর বিচরণ দৃশ্যমান। আবার বছরে গৃহস্থালী শ্রমে নারী প্রায় ১০-১২ কোটি টাকার মূল্য তৈরি করে যার কোন স্বীকৃতি পরিবার,সমাজ ও রাষ্ট্রে নেই। কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে নারীর অংশগ্রহণ বেশি। দেশের প্রধান শিল্পখাত গার্মেন্ট। এই খাতের ৮০ ভাগই নারী শ্রমিক।
৯ লাখ নারী গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করছে। কৃষি কাজে ৯০ লাখ ১১ হাজার নারী নিয়োজিত। আর নিজ কর্মক্ষেত্রের বাইরের নারী পরিবারে রান্না, সন্তান লালন-পালনসহ গৃহস্থালী কাজে প্রায় প্রতিদিন সাড়ে তিন ঘন্টা সময় ব্যয় করেন। ঠিক তার বিপরীতে আছে নারীর উপর ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। ৮৭ শতাংশ বিবাহিত নারী নিজ গৃহেই নির্যাতনের শিকার হয়। বাল্যবিবাহের হার ৬৫ শতাংশ। ৮০ শতাংশ অবিবাহিত নারী যৌন হয়রানির শিকার। এছাড়া ধর্ষণ-গণধর্ষণ, যৌতুক ও এসিড নিক্ষেপের কারণে নারী হত্যার শিকার হয়। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় আইন ব্যর্থ।
মূলত সরকারের পরিসংখ্যান মতে নারীর অগ্রগতি এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে হলেও পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনের এই বৈষম্য বিলোপ করতে হবে।
রাষ্ট্রের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনে পার্থক্য বিদ্যমান। তাই এই পার্থক্য দূরীকরণে পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনসমূহকেও দেওয়ানী আইন ও আদালতের আওতায় এনে ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রবর্তন করে পারিবারিক আইনের বৈষম্য দূর করতে হবে।
ফলে সরকার যদি সিডও সনদ, সংবিধান এবং অন্যান্য আর্ন্তজাতিক আইনের আলোকে সমাজে বিরাজমান বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে তাহলে সমাজে নারীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিবর্তন ঘটবে।যদিও শ্রেণীবিভক্ত এই সমাজে রাষ্ট্র তার নিজের প্রয়োজনে আইন তৈরি করে। ফলে বিদ্যমান এই সমাজ কাঠামোতে সত্যিকার অর্থে নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব। তাই নারীর সত্যিকার মুক্তি কেবলমাত্র একটি শোষণহীন সমাজেই সম্ভব। এই শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারী-পুরুষের মিলিত অংশগ্রহণই আমাদের কাম্য।
তথ্যসূত্রঃ
পারিবারিক আইনে বাংলাদেশের নারী – আইন ও সালিশ কেন্দ্র
নারী বিষয়ক আইন-কানুন – মোঃ আব্দুল হান্নান ও মোঃ মতিউল ইসলাম সম্পাদিত
নারী অধিকার ও কয়েকটি আইন – তাহমিনা হক
আরও পড়ুন …
ধর্ষক এর পারিবারিক ও সামাজিক আশ্রয়
নারীকে বলতে হয় আমি মানুষ! ——— কনক আধিয়ার