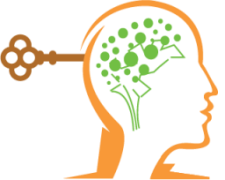—– Shahiduzzaman Fahim
****************** **************
সারসংক্ষেপ: একজন বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক ও প্রতিবাদী চেতনার কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী। ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় থাকা এই প্রতিভাবান কবি কেবল রাজপথে নয়, কলমেও প্রকাশ করেছেন পরাধীনতার হাহাকার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার তীব্র ধ্বনি। ৫২’র ভাষা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে রচিত তাঁর অন্যতম জ্বালাময়ী কবিতা ❝কাঁদতে আসেনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি❞। সময়ের ব্যবধানে এই ফাঁসির দাবি কেবল তৎকালীন ভাষা আন্দোলনকে প্রতিনিধিত্ব করে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই ফাঁসির দাবি প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম হয়ে যুগের পর যুগ অধিকারহারা মানবের স্বাধিকার আদায়ের দাবি এবং স্বাধিকার নিয়ে বাঁচার দাবি হয়ে উঠেছে। কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর উক্ত কবিতাকে অবলম্বন করে আলোচ্য প্রবন্ধে তৎকালীন ও সমকালীন সংগ্রামী চেতনার প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।
বিশিষ্ট মার্কিন রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রর একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিঁনি বলেছেন, ‘Democracy is a government of the people, by the people, for the people’- অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের অংশগ্রহণ, জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য। তৎকালীন পাকিস্তান অধিরাজ্যের দুইটি অংশ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান। প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পাকিস্তানের দুইটি অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য বিরাজমান ছিল। বলা হয়ে থাকে, তৎকালীন পাকিস্তানের শতকরা ৫৬.৪ ভাগ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু তবুও পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। আমরা বলতে পারি মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা এবং একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্তই ছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রধান ও প্রকাশ্য অগণতান্ত্রিক আচরণ।
ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার নদী ও জীবন যেমন এখানকার মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামমুখর জীবনের কথা স্মরণ করে দেয়, ঠিক তেমনই স্বাধিকার আদায়ের জন্যও এই বাংলার সর্বস্তরের মানুষকে লড়তে হয়েছে যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর। ৫২’র ভাষা আন্দোলন আমাদের স্পষ্ট করে দেয় পূর্ব বাংলার মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ারও বহু বছর আগে থেকেই তাদের অধিকারের প্রতি সচেষ্ট ছিল। ভাষা আন্দোলনের মূল দাবিটা ছিল ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’। এখানে ‘রাষ্ট্রভাষা’ বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালিত হওয়ার ভাষা। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের একটি বক্তব্যের কথা উল্লেখ করা যায়। ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’ নামক গ্রন্থে তিঁনি বলেছেন:
❝গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের মুখের ভাষা
রাষ্ট্র-ভাষা হইবে, এটা বুঝিতে প্রতিভার
দরকার হয় না। সবাই এটা বুঝিয়াছিলেন।
আমাদের মত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কর্মীরা মুখ ফুটিয়া
তা বহু আগে বলিয়াছিলামও।…পাকিস্তানের
মেজরিটির ভাষা বাংলাকে আগ্রাহ্য করিয়া
উর্দুর ডবল মার্চ চলিতে থাকে। ক্ষমতাসীন
দলের পূর্ব-বাংগালী মন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা এর
প্রতিবাদে বা বাংলার সমর্থনে টু শব্দটি
করেন না। এতেই ১৯৫২ সালের ২১ শে
ফেব্রুয়ারিতে বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে।❞ ১
ঠিক সেই সময়েই কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন একুশের প্রথম কবিতার। প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন গণ-জাগরণের।
‘কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি’ কবিতাটির প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পংক্তির দিকে দৃষ্টি রাখলে দেখা যায়:
❝আজ আমি শোকে বিহ্বল নই
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই
আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল।❞ ২
উপর্যুক্ত পংক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, লেখকের এই প্রতিজ্ঞার অন্যতম কারণ তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক দীর্ঘদিনের নির্বিচার, হত্যা, লুণ্ঠন ও অগণতান্ত্রিক আচরণ। কবির এই প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে দুটো বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে।
ক) অধিকারহার বাঙালি জাতির মনোবলকে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা।
খ) শোকে বিহ্বল ও ক্রোধে উন্মত্ত বাঙালি জাতির একটি গণ-জাগরণ প্রত্যাশা।
এক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের মার্কসবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী ও প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিবাদী চেতনাকে স্মরণ করা যায়। তিঁনি “পূর্বাভাস” কাব্যের ‘দুর্মর’ কবিতায় বলেছেন:
❝ সাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়:
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।❞ ৩
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিঁনি যে স্বোচ্ছার ছিলেন, তার পরিচয় এরূপ বিভিন্ন কবিতায় পাওয়া যায়। সমকালীন স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণ করলেও যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়, তা হলো:
ক) সরকার ও জনগণের চাহিদার অনৈক্য।
খ) অগণতান্ত্রিক মনোভাব।
গ) অস্থিতিশীল আইন ও বিচার ব্যবস্থা।
আর তাই রাজপথে অধিকার আদায়ের মিছিলে স্বৈরশাসকের বুলেটের সম্মুখেও দাঁড়াতে দেখা যায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের মতো সহস্র তরুণকে। প্রজন্মের এই আত্মত্যাগ আমাদের স্মরণ করে দেয় ৫২’এর ভাষাশহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জাব্বারসহ অগণিত বীরদের কথা।
মাহবুব উল আলম চৌধুরীর উক্ত কবিতায় দেখা যায়, বীরেরা প্রাণ দিয়েছেন-
ক) মাতৃভাষা বাংলার জন্য।
খ) দেশের সংস্কৃতির মর্যাদার জন্য।
গ) আলাওল, রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, নজরুল প্রবৃতি সাহিত্যিকের সাহিত্য, ঐতিহ্য ও কবিতার জন্য।
ঘ) পলাশপুরের মকবুল আহমদের পুঁথির জন্য।
ঙ) রমেশশীলের গাঁথার জন্য।
চ) জসীমউদদীনের সোজন বাদিয়ার ঘাটের জন্য।
এখানে স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং আধিপত্যবাদের প্রতি ধিক্কার জানানোর পাশাপাশি স্বদেশের সংস্কৃতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বীরদের আত্মত্যাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনুরূপভাবে ২৪’র জুলাই অভ্যুত্থানে তরুণ প্রজন্মের মুখে মুখে শোনা যায় ‘দিল্লী না ঢাকা ? ঢাকা, ঢাকা’- প্রভৃতি আধিপত্যবাদ বিরোধী স্লোগান। এখানে ভারতীয় আগ্রাসন থেকে স্বদেশকে মুক্ত রাখার তীব্র ক্ষোভ এবং স্বদেশের স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।
কবিতায় আছে:
❝ অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত
বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সেরা কোনো
ছেলের বুকের রক্ত।❞ ৪
ভাষাতাত্ত্বিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাজপথে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য শিক্ষার্থী তাজা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষা। তদ্রূপ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও স্বাধীন দেশের স্বপক্ষে কলম ধরায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবরারকে প্রাণ দিতে হয়েছে স্বৈরশাসকের ঘাতকদের হাতে। প্রজন্মের এই সংগ্রামী আত্মত্যাগ বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন কবির কবিতার বারংবার পাওয়া যায়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন:
❝ধ্বংস দেখে ভয় কেনো তোর ?- প্রলয় নূতন সৃজন-
বেদন!
আসছে নবীন-জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে
ছেদন! ❞ ৫
আর সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় একই সুর বাজতে দেখা যায়:
❝এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।❞ ৬
এখানে প্রকাশিত হয়েছে ক) তারুণ্যের আহ্বান খ) সংগ্রামী জীবনের প্রতি তারুণ্যের কোলাহল।
এই তরুণ প্রজন্মই ৫২’র ভাষা আন্দোলন, ৬৯’র গণ-অভ্যুত্থান, ৭১’র মহান মুক্তিযুদ্ধ এমনকি স্বাধীন স্বদেশের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ২৪’র গণ-অভ্যুত্থান এনে দিয়েছে।
একুশের প্রথম কবিতায় কবি বলেছেন:
❝আমি তাদের ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি
যারা আমার ভাই বোনকে
নির্বিচারে হত্যা করেছে।❞ ৭
পাঠক সমাজে কাছে প্রশ্ন জাগতেই পারে এতো এতো অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই ফাঁসির দাবি নিয়ে কবি মূলত কার কাছে এসেছেন ? কবির এই ফাঁসির দাবি কে মেনে নিবে ? কবির এই দাবি মূলত সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার দাবি, একটি অনাগত বিপ্লবের দাবি। যারা বাঙালি সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করতে চেয়েছে, মাতৃভাষার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে চেয়েছে, তাজা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, কবি সেই ঘাতকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী গণ-জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন।
তদ্রূপ স্বদেশে স্বাধিকার রক্ষায় স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে ২৪’র গণ-অভ্যুত্থান এবং এক দফা এক দাবির আন্দোলন যেনো কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কবিতায় অগণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফাঁসির দাবি উত্থাপনের সাথে প্রাসঙ্গিক।
তথ্যনির্দেশ:
১) আবুল মনসুর আহমদ, ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’ খোরশেদ কিতাব মহল, ১৫-বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০, পৃষ্ঠা: ২৪৯।
২) মাহবুব উল আলম চৌধুরী ‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।’
৩) সুকান্ত ভট্টাচার্য, “পূর্বাভাস” কাব্য, ‘দুর্মর’ কবিতা, জয় প্রকাশন।
৪) মাহবুব উল আলম চৌধুরী ‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।’
৫) কাজী নজরুল ইসলাম, “অগ্নি-বীণা” কাব্য, ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতা।
৬) সুকান্ত ভট্টাচার্য, “ছাড়পত্র” কাব্য, ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতা।
৭) মাহবুব উল আলম চৌধুরী, ‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।’